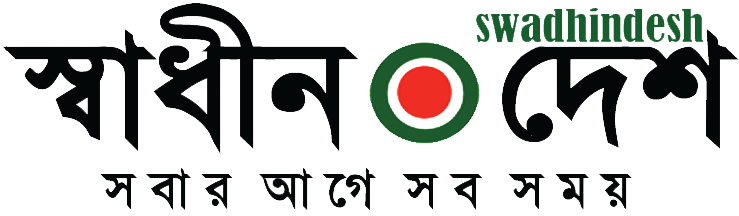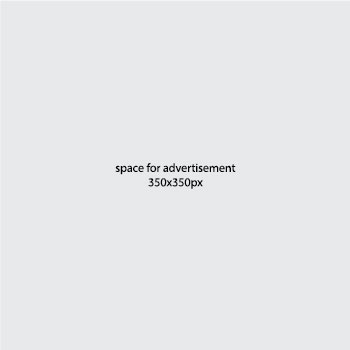রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান হয়েও তৃণমূল থেকে উঠে আসা রাজনীতিবিদ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ষাটের দশকে ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি হয়ে মাঠে লড়াই করেছেন, অস্ত্র হাতে সমাজ পরিবর্তনে গিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। পেশায় সরকারি কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন।
প্রশ্ন : বাম রাজনীতির প্রতি আগ্রহ কিভাবে জন্মাল?
রাজনৈতিক পরিবারে আমার জন্ম, ঠাকুরগাঁও শহরের মানুষ। বাবা মরহুম মির্জা রুহুল আমিন, ‘চখা মিঞা’ পাকিস্তান আমলে মুসলিম লীগের বড় নেতা ছিলেন, ঠাকুরগাঁও পৌরসভার নির্বাচিত চেয়ারম্যান। ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে আমি ছাত্রজীবনেই বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। ১৯৬২ সালে ঠাকুরগাঁও হাই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিলাম। সে বছরই ঠাকুরগাঁও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
আমাদের স্কুলের এক অংশে সকালে কলেজের ক্লাস হতো। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক প্রয়াত শওকত আলী বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর জীবনে প্রথম পোস্টিং। প্রায় দিনই স্কুলে ক্লাস করতে ঢোকার সময় দেখতাম স্যার বারান্দায় বসে আছেন। কবিতা আবৃত্তি করি, নাটক করি, ছাত্র হিসেবেও ভালো বলে আমাকে খুব পছন্দ করতেন। একদিন ডেকে বললেন, ‘তোমার হাতে এগুলো কী বই?’ সে আমলের জনপ্রিয় গোয়েন্দা সিরিজ ‘স্বপন কুমার’সহ আরো কিছু বই—হালকা রোমান্টিক উপন্যাস ছিল। উল্টেপাল্টে দেখে বললেন, ‘সবই দেখি হালকা রচনা!’ ‘স্যার, ছোটবেলা থেকে বই পড়তে ভালোবাসি। ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণিতেই শরত্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস পড়ে ফেলেছি, রবীন্দ্রনাথের গল্প-কবিতা-উপন্যাস পড়তে ভালোবাসি। ’ ‘তাহলে এগুলো কেন পড়ো? কী শেখো? খুন, হত্যা, খারাপ সম্পর্ক, চক্রান্ত—ছাড়া তো এসবে ভালো কিছু নেই। শুধু এসবই পড়ো না। ’ এরপর স্যার কয়েকটি বই পড়তে দিলেন। সেগুলোর মধ্যে একটি—নীহারকুমার সরকারের ‘ছোটদের রাজনীতি’। বইটিতে ছোটদের ভাষায় খুব সুন্দর করে পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ আলোচনা করা হয়েছে। এই একটি বই-ই আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। বইটি খুব আলোড়িত করেছে। আমার চিন্তা-চেতনাকে বদলে দিল। প্রথম বিভাগে এসএসসি পাস করে এর পর ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হলাম।
প্রশ্ন : কলেজে কাদের পেলেন?
তখন পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে অগ্রসর ছাত্ররা ঢাকা কলেজে পড়ত। উচ্চ মাধ্যমিকে পড়লেও তাদের জ্ঞানের গভীরতা ছিল অসাধারণ। আমার সহপাঠীদের অন্যতম ড. আহমেদ কামাল সে আমলেই প্রচুর পড়ত। ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ তো বরাবরই রেকর্ড মার্কস নিয়ে প্রথম হয়েছে। তাদের সংস্পর্শে এসে, শওকত ওসমান, নোমান স্যারের সাহচর্যে বই পড়ার ঝোঁক আরো বেড়ে গেল, বাম রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ হলো। একদিন বন্ধু বাবলা বলল, ‘রাশেদ খান মেননের সঙ্গে পরিচিত হবে?’ তিনি তখন অবিভক্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ডাকসু’র ভিপি, তখনই কিংবদন্তি ছাত্রনেতা। সে সময় তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া আমাদের মতো সাধারণ ছাত্রের জন্য বিরাট বিষয়। যেখানে এখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, তখন সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন ছিল। বাবলা নিয়ে গেল। মেনন ভাই চা খাচ্ছেন। ডাক শুনে উঠে এলেন। আমার শার্টের ওপরের বোতামটি খোলা ছিল। কথা বলতে বলতে তিনি বোতামটি লাগিয়ে দিলেন। এত বড় একজন নেতা নিজের হাতে আমার বোতাম লাগিয়ে দিয়েছেন! মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ফলে ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে ছাত্ররাজনীতির আকর্ষণ বাড়ল; কিন্তু ঢাকা কলেজের কোনো ছাত্রেরই তখন রাজনৈতিক জীবন ছিল না। তখন সামরিক সরকার আইয়ুব খান, মোনেম খাঁর আমলে নিষেধাজ্ঞা ছিল—রাজনীতি, সংগঠন কিছুই করা যাবে না। প্রবল প্রতাপশালী নামকরা শিক্ষক জালাল উদ্দিন স্যার আমাদের প্রিন্সিপাল, আন্দোলন দমনে খগড়হস্ত। আমাদের কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই করতে দিতেন না। তিনি প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের শ্বশুর, আইভি রহমানের বাবা। আমি নর্থ হোস্টেলে থাকলেও রাজনীতি করতে পারিনি; কিন্তু ১৯৬৪ সালে ঢাকায় রায়ট হলো। তখন কোনো বাধা না মেনে রায়টের বিরুদ্ধে মিছিল করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছি।
প্রশ্ন : মুসলিম লীগের নেতা বাবা তাঁর ছেলের বাম রাজনীতি কিভাবে দেখতেন?
তখন তো সব অগ্রসর, আধুনিক মানুষরা মুসলিম লীগ করতেন। তবে কোনো বাবাই বোধ হয় চান না তাঁর সন্তান রাজনীতি করুক। ঘটনাপরম্পরায় হয়ে যায়। বাবা বাধা না দিলেও মায়ের (ফাতেমা আমিন) কাছে আক্ষেপ করে বলতেন, ‘আমার ছেলেটি ভালো ছিল, রাজনীতি করে বোধ হয় নষ্ট হয়ে গেল। ’ বাবার খুব ইচ্ছা ছিল, আমি ব্যারিস্টার বা সিএসএস (পাকিস্তান সেন্ট্রাল সার্ভিস কমিশন) পরীক্ষা দিয়ে সরকারি বড় অফিসার হই। কোনোটিই করতে পারিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে তো ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করলাম। লন্ডনে বার অ্যাট ল পড়ার জন্য ভর্তি নিশ্চিত হয়েছিল; কিন্তু সেখানে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।
প্রশ্ন : অর্থনীতিতে কেন ভর্তি হলেন?
বাবা মনে করেছিলেন, অর্থনীতিতে ভর্তি হলে আমার ভবিষ্যৎ ভালো হবে। আমাদের সময় কলা অনুষদের সবচেয়ে ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা অর্থনীতি, ইংরেজি, ইতিহাসের মতো বিষয় পড়তে চাইত। ফলে ১৯৬৫ সালে অর্থনীতিতে ভর্তি হলাম। বিভাগে অনেক উজ্জ্বল শিক্ষক ও ছাত্র পেয়েছি। ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, অভিনেতা গোলাম মোস্তফা ভাই ও মেধাবী ছাত্র আবদুল্লাহ, নামকরা ছাত্র ও পরে অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহকে বিভাগে বন্ধু, ছাত্র হিসেবে পেয়েছি। ড. আকবর আলি খান আমাদের সময় ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন।
প্রশ্ন : রাজনীতিতে কেন যুক্ত হলেন?
ষাটের দশক তো রাজনীতির কাল। চীন, ভিয়েতনামসহ পুরো বিশ্বে বিপ্লবের হাওয়া বইছে; পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানিদের শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন চলছে। আগেই বলেছি, আমার বাবা রাজনীতিবিদ, চাচা মির্জা গোলাম হাফিজ পরে বিএনপির স্পিকারও হয়েছেন, বৃহত্তর দিনাজপুরের বালুবাড়িতে চাচা কাদের বক্স সাহেবের ছেলে মির্জা নুরুল হুদা সাচ্চা কমিউনিস্ট ছিলেন, বড় মামা ইউসুফ সাহেব দিনাজপুর জেলা কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁরা সবাই আমাকে খুব প্রভাবিত করেছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই রাজনীতি করব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। এসেই এসএম (সলিমুল্লাহ মুসলিম হল) হল শাখার ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারি নির্বাচিত হলাম। এর পর ছেষট্টির ছয় দফা থেকে ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন—প্রতিটি সংগ্রামেই আমি ও আমার রাজনৈতিক বন্ধুরা সক্রিয় আন্দোলন করেছি। প্রতিটি মিছিলে গিয়েছি, সভা করেছি, ছাত্র ইউনিয়নের হয়ে সারা দেশের সব জেলায় ঘুরে বাঙালির অধিকারের আন্দোলন সংগঠিত করেছি।
প্রশ্ন : সেই সময়ের উল্লেখযোগ্য স্মৃতি?
সরকারি ছাত্র সংগঠন এনএসএফ (ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন) তখন খুব প্রতাবশালী, আমাদের ওপর খুব অত্যাচার-নির্যাতন করত। আন্দোলনে গেলে আমাদের রুম পুড়িয়ে দিত, কর্মীদের রুম থেকে বের করে দিত। আমাদের বিভাগের প্রধান আবু মাহমুদ খুব বিদ্রোহী মানুষ ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে একটি মামলা করার পর এনএসএফের গুণ্ডারা তাঁকে খুব মারধর করল। স্যার রক্তাক্ত হয়ে গেলেন। শিক্ষকের ওপর হামলার প্রতিবাদে আমরা রাজপথে নেমে গেলাম। বিষয়টি অনেক দূর গড়ালে আমাদের হল পর্যন্ত ছাড়তে হলো। এ নিয়ে বিরোধের প্রেক্ষাপটে তো ইউনিয়নের কর্মীদের হাতে এনএসএফের অন্যতম পাণ্ডা সাইদুর রহমান পাঁচপাত্তু মারা গেল। হলেই তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছিল, আহত হয়ে পরে সে মারা গেল। এরপর হলে পুলিশের রেইড হলো। আমাদের হলছাড়া করে দেওয়া হলো। তখন আমরা বিশ্ববিদ্যালয়েই ঢুকতে পারতাম না, পা দিলেই আক্রমণের শিকার হতাম। ১৯৬৮ সালে অনার্স শেষ হয়ে গেল। ফলে প্রায় ২০-২৫ জন ছাত্র সিদ্ধান্ত নিলাম, বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিতে হবে। সে বছরের শেষের দিকে মাস্টার্স করতে বৃত্তি নিয়ে করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। ওয়াহিদ, আনিস (আনিসুল ইসলাম মাহমুদ) ইসলামাবাদ ইউনিভার্সিটিতে গেল। আমি হলে থাকতাম। ঊনসত্তরে ঢাকার উত্তাল আন্দোলনের ঢেউ করাচিতেও পৌঁছে গেছে। সেখানেও বড় আন্দোলন হয়েছে, সে আন্দোলনে অংশ নিয়েছি, মিছিলে বক্তৃতা করেছি। আমাদের আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল। আন্দোলন করায় ‘ট্রান্সফার সার্টিফিকেট’ নিয়ে আমাকে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসতে হলো। ঢাকায় পা রেখেই আন্দোলনে জড়িয়ে গেলাম। সেই সময় ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিটি আন্দোলনে আমরা নেতৃত্ব দিয়েছি। আমি ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ছিলাম। এখনো মনে আছে—১৯৭০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর আমরাই প্রথম ইয়াহিয়া খানের ‘মার্শাল ল’ ভেঙে রাজপথে নেমেছি। তাতে পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে, রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে রেইড দিয়েছে। বাধ্য হয়ে আমরা পালিয়ে গেলাম। এর মধ্যেই ১৯৭০ সালে মাস্টার্সের ফল প্রকাশিত হলো। ছাত্রত্ব শেষ হয়ে যাওয়ায় বাড়ি চলে গেলাম। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী) সঙ্গে যুক্ত হয়ে দিনাজপুর জেলা শাখার প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হলাম। দল আমাকে ডাকসু নির্বাচনের প্রস্তাব দিল; কিন্তু ১৯৬৪ সালেই তো ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া-মেনন গ্রুপে ভাগ হয়েছে, একটি শব্দ নিয়ে তো বামপন্থীরা ভাগ হয়ে যান, কমিউনিস্টদের মধ্যে এত কোন্দল আর সশস্ত্র বিপ্লবের ডাক এসেছে বলে বিপ্লব করতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।
প্রশ্ন : বিপ্লবের দিনগুলো?
দেবেন শিকদার, ভাষা মতিনের নেতৃত্বে আমরা প্রাথমিকভাবে বিপ্লবীদের সংগঠিত করতে চেষ্টা করছি। ভালো নাম শামসুজ্জোহা, তবে ‘মানিক ভাই’ নামে সবাই চেনেন, তিনি তখন ভারতীয় সীমান্তের কাছে, নদীর ধারে পঞ্চগড়ের হাড়িভাসা গ্রামে কৃষক আন্দোলন করছেন। এই কমিউনিস্ট নেতাই আমাদের প্রধান ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনে জড়িয়ে গেলাম। সেই গণ্ডগ্রামে কৃষকদের বাড়িতে থাকতাম, খেতাম, তাঁদের সংগঠিত করতাম। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসের (ইপিআর) কয়েকটি বন্দুক ছিনিয়ে কার্তুজও তৈরি করা হলো। কিন্তু আমরা দেখলাম, এটি পুরোপুরি ভুল পথ। ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিপ্লবের চেষ্টা বা শ্রেণিশত্রু খতম করে কখনো বিপ্লব করা যায় না। সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়েই বিপ্লব করতে হয়, শেখ সাহেব নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় নেতা হয়ে উঠলেন। ফলে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনে জনগণের সমর্থন পেলাম না। এরপর একাত্তরের মার্চে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলো, সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আন্দোলনে যোগ দিলাম।
প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধকে কিভাবে সংগঠিত করলেন?
২৫শে মার্চ ঢাকায় গণহত্যার পর ঠাকুরগাঁওয়ে হাজার হাজার মানুষ নিয়ে আমরা ইপিআর ক্যাম্প ঘেরাও করলাম। তখন সেখানে এক ব্যাটালিয়ন সৈনিক ছিল। ঘণ্টা দুয়েক তারা গোলাগুলি করল। ঘটনাস্থলে মোহাম্মদ আলী নামে আমাদের একজন শহীদ হলেন। তিনি পেশায় রিকশাচালক ছিলেন, ঠাকুরগাঁওয়ের প্রথম শহীদ। তাঁর কবর আছে, তাঁর নামে সড়ক আছে। ঘটনাস্থলে নরেশ চৌহান শহীদ হলেন। তুমুল উত্তেজনার মধ্যে আমরা আত্মগোপনে চলে গেলাম ও তেঁতুলিয়া সীমান্তের কাছে জড়ো হলাম; কিন্তু এর মধ্যে ঠাকুরগাঁওয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক কম্পানি ও ইপিআর সদস্যরা কন্ট্রোলরুম তৈরি করে আশরাফ সাহেব, ক্যাপ্টেন কাজিম উদ্দিন, আমার চাচা উইং কমান্ডার এহসান মির্জা ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কন্ট্রোলরুম তৈরি করে বাঙালিদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয়েছেন। ফলে আবার ফিরে এলাম। তাদের অস্ত্রভাণ্ডার থেকে সব রাইফেল নিয়ে নিলাম এবং তরুণদের ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দিলাম। ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। ১৪ এপ্রিল পাক আর্মি সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে আমাদের ওপর রকেট লঞ্চার ছুড়তে লাগল। বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআরের ভাইয়েরা প্রথম দিকে প্রবল বাধা দিলেন; কিন্তু উন্নত অস্ত্রের সঙ্গে না পেরে পিছু হটে পঞ্চগড় থেকে তেঁতুলিয়ার মাঝখানে ভজনপুরে ডিফেন্স তৈরি করলেন। তাঁদের সঙ্গে আমরাও ছিলাম। ঠাকুরগাঁওয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ছড়িয়ে পড়লে সীমান্ত পেরোতে হলো। পঞ্চগড়ের আটোয়ারী থানার সুকাতি গ্রাম দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে আমি, পঞ্চগড়ের এমপি সিরাজুল ইসলাম, আমার চাচা এস আর মির্জা, লাল সাহেব, আওয়ামী লীগের জেলা সেক্রেটারি মীর্জা রফিকুল ইসলাম, ছাত্রলীগ নেতা নুরুল ইসলাম ভারতের পশ্চিম দিনাজপুরের সাবডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার্স ইসলামপুর চলে গেলাম। সেখানে কয়েক দিন ছিলাম। দিলীপ, সিপিএমের নেতা বাচ্চা মুন্সির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলো। তাঁরা আমাদের স্কুলে থাকার জায়গা করে দিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সিপিএম নেতা, এমপিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম।
প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের জীবন?
বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কর্পুরি ঠাকুর আমাদের যুবকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য তাঁবু, জামাকাপড়, বুট ইত্যাদি দিলেন। থাকুরাবাড়িতে আমরা ক্যাম্প তৈরি করলাম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ হলো। তারা ক্যাম্প তৈরি করতে দিল। সেই ক্যাম্পে যুবকদের জড়ো করে আমরা মুক্তিযুদ্ধে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করে পাঠালাম। ৯ মাস এভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেছি। মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট, প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রেরণ, তাদের নানা সমস্যার সমাধান ইত্যাদি কাজ করতে হয়েছে। যেহেতু বাম ঘরানার ছিলাম, আওয়ামী লীগের লোকেরা সেভাবে আমাদের বিশ্বাস করত না, এখনো করে না। ফলে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল ফ্রন্ট গঠন করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ করতে হয়েছে। আমার সঙ্গে হায়দার আকবর খান রনো, রাশেদ খান মেনন ভাই প্রমুখের দেখা হয়েছে, আমরা সভা করেছি। তখন ইসলামপুর যুব ক্লাবে থাকতাম। এটি সিপিএমের যুব সংগঠন ছিল। ৩ ডিসেম্বর ঠাকুরগাঁও স্বাধীন হলো। আমি ১০ ডিসেম্বর দেশে চলে এলাম। এটা তখন বিধ্বস্ত জনপদ। আমাদের বাড়ির বৈদ্যুতিক লাইনগুলো পর্যন্ত ওরা খুলে নিয়ে গেছে। পেট্রল পাম্প তছনছ করে ট্যাংক, সিনেমা হলের প্রজেক্টর, ট্রাক—সব কিছু রংপুর ও সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গেছে। খুঁজে খুঁজে সেগুলো আনতে হয়েছে। মা-বাবা ইসলামপুরের ভাড়া বাসা থেকে চলে এলেন। বড় বোন, তাঁর স্বামী, পরে সেনাপ্রধান জেনারেল মাহবুবুর রহমানের সঙ্গে পাকিস্তানে বন্দি ছিলেন।
প্রশ্ন : ফিরে আসার পর কী করলেন?
তখন আমাদের কোনো আয় ছিল না। ১৯৭০ সালের অক্টোবরে কেবিএম (কাদের বকশ মেমোরিয়াল) কলেজে অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম। সেখান থেকে বেতন, এরিয়ারের টাকাও সংসার চালানোর জন্য মায়ের হাতে তুলে দিতে হতো। ১৯৭০ সালেই তো সিএসএস পরীক্ষা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম। স্বাধীনতার পর খুলনার বিএল কলেজে অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগপত্র এলো; কিন্তু সংসারের এ অবস্থায় চিঠি লিখে জানাতে হলো—পরিবারের এ অবস্থায় আমার পক্ষে এখন খুলনায় যাওয়া সম্ভব নয়। ফলে তারা দয়াপরবশ হয়ে আমাকে দিনাজপুর সরকারি কলেজে বদলি করলেন। পরিবারের এই অবস্থা—আর হয় আওয়ামী লীগ করো, নয়তো চুপ করে বসে থাক—এই অবস্থা হলো বলে আর রাজনীতির দিকে গেলাম না। ১৯৭২ সালের ১৮ জুন সরকারি স্কেল অনুসারে ৪৫০ টাকা বেতনে চাকরিতে যোগ দিলাম। বাড়ি থেকে ৩৬ মাইল ভাঙ্গা ব্রিজ, ফেরি পার হয়ে যেতে-আসতে সাড়ে তিন ঘণ্টা করে লাগত। দেড় বছর এভাবে শিক্ষকতা করলাম। এরপর বদলি হয়ে ঢাকা কলেজে চলে এলাম। ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে যোগ দিয়ে ১৯৭৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত এখানে ছিলাম। এরপর আবার দিনাজপুর সরকারি কলেজে যোগ দিলাম।
প্রশ্ন : সরকারি কর্মকর্তা কিভাবে হলেন?
১৯৭৬ সালে ডেপুটেশনে ইউনেসকো ন্যাশনাল কমিশনে প্রগ্রাম অফিসার হিসেবে যোগ দিলাম। ততদিনে জিয়াউর রহমানের কেবিনেট গঠিত হয়েছে। সে বছরের জুনে পারিবারিকভাবে বিয়ে হলো—স্ত্রী রাহাত আরা পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক, এখন ডেল্টা লাইফ ইনস্যুরেন্সের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত আছে। আমাদের দুই মেয়ে—মীর্জা শামারূহ ও মীর্জা সাফারূহ। দুজনই শিক্ষক। শামারূহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগের শিক্ষক ছিল, অস্ট্রেলিয়ায় পিএইচডি করে, সেখানে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত আছে। তার স্বামী আবুল কালাম ফাহমিও একই বিভাগে পিএইচডি করেছে। তারা ওই দেশের নাগরিকত্ব পেয়েছে। আর ছোট মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স, সানিডেল স্কুলের শিক্ষক; তার স্বামী আদনান সাবের গ্রামীণফোনে কর্মরত।
প্রশ্ন : ইউনেসকো ন্যাশনাল কমিশনে কী কাজ করতেন?
ইউনেসকো শিক্ষাবিষয়ক যেসব প্রগ্রামের সঙ্গে জড়িত, সেগুলোর আরো উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রজেক্ট নেওয়ার কাজ করতাম। এসএ বারী উপপ্রধানমন্ত্রী থাকার সময় ডেপুটেশনে তাঁর পিএস (ব্যক্তিগত সচিব) নিযুক্ত হলাম। তাঁর হয়ে নির্বাচন করতে গিয়ে ১৯৭৯ সালেই আমি পুরো দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁওয়ের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল নিজের হাতে তৈরি করেছি। নাট্য সংগঠনসহ সব সংগঠন তখনই আমার হাতে তৈরি হয়েছে। তখন ঢাকায় শেরেবাংলানগর এমপি হোস্টেলে থাকতাম। তখন আমার বাবা এমপি ছিলেন, তাঁর নামে হোস্টেলে একটি ‘স্যুট’ ছিল। এক রুমে তিনি থাকতেন, আরেক রুমে আমি, আমার স্ত্রী ও দেড় বছরের বড় মেয়ে থাকতাম। তখনই সরকারের কার্যক্রম খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেলাম এবং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কর্মে তাঁর ভক্ত হয়ে গেলাম।
প্রশ্ন : তিনি কেমন ছিলেন?
তিনি অনেক কাজ করেছেন। যেমন—তিনি সকাল সাড়ে ৭টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত অফিসের সময় নির্ধারণ করলেন। মন্ত্রীরা কারা সময়মতো আসছেন, কারা আসছেন না দেখার জন্য নিজেই সচিবালয়ের গেটে দাঁড়িয়ে থাকতেন। পুরো দেশের মানুষকে সংগঠিত করতে গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন, অনেক রাত অবধি কাজ করতেন। প্রচণ্ড হতাশ জনসাধারণকে তিনি জাগ্রত করার চেষ্টা করেছিলেন। উত্পাদন বাড়ানো ও জেলাগুলোর সমস্যা সমাধানের জন্য জেলাগুলোর সার্কিট হাউসগুলোতে কেবিনেট মিটিং করতেন, উপস্থিত সিদ্ধান্ত দিতেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে গোটা জাতিকে তিনি উন্নয়নের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে আমি মনে করি। তিনি সবাইকে নিয়ে একাত্ম হতে চেয়েছিলেন বলে গণতন্ত্রের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। জাতীয় ঐক্য তৈরি করেছিলেন এবং মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু করেছিলেন।
প্রশ্ন ; তাঁর সঙ্গে কোনো স্মৃতি আছে?
তিনি তো ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানুষের সঙ্গে খুব মিশতেন, সব কিছু সামগ্রিকভাবে দেখতেন। তিনি কয়েকবারই দিনাজপুর এসেছিলেন। একবার দিনাজপুরে আসবেন। তখন ঠাকুরগাঁওয়ে বিমানবন্দর ছিল। আমরা তাঁর গাড়িবহরের জন্য অপেক্ষা করছি, খাওয়া প্রস্তুত। হঠাৎ একটি জিপ দ্রুত প্রবেশ করল। তিনি নিজে ড্রাইভ করছেন, পাশে দিনাজপুরের ডিসি। গাড়ি থেকে চট করে নেমে গার্ড অব অনার নিয়ে টপটপ করে ওপরে উঠে গেলেন। ১৫ মিনিট পর অন্য গাড়িগুলো এলো। এর মধ্যে তিনি খাওয়া শেষ করে নেমে গেছেন। অন্যদের খাওয়া শেষ না করেই চলে যেতে হলো। রাতে খুব কম ঘুমাতেন। বেশ কয়েকবার দিনাজপুর সার্কিট হাউসে থেকেছেন। তখন দেখেছি, স্থানীয় নেতা, এমপি, ছাত্রনেতা সবার সঙ্গে কার্পেটে বসে তিনি তাদের সমস্যার সমাধান দিতেন। আমাদের দিনাজপুর সরকারি কলেজের ভিপি এক মিটিংয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—‘স্যার, আমাদের একটি রঙিন টেলিভিশন দরকার। ’ তিনি খুব রেগে গিয়ে বললেন, ‘তুমি কলেজের ভিপি, তুমি প্রেসিডেন্টের কাছে রঙিন টিভি চাইছ? বিজ্ঞান ভবন বা অডিটরিয়াম কেন চাওনি?’ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটাই এমন ছিল। খুব দ্রুত কাজ করতে পারতেন।
প্রশ্ন : মন্ত্রণালয় ছেড়ে দিলেন কেন?
তিনি মারা যাওয়ার পর বিচারপতি সাত্তার সাহেবের মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। তিনি প্রধানত মুক্তিযোদ্ধাদের মন্ত্রী হিসেবে নিলেন না। ফলে বারী সাহেবও রইলেন না। সেই মত্স্য মন্ত্রণালয়ে আবুল কালাম এলেন। তাঁর পিএস হিসেবে কাজ করেছি। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এরশাদ ক্ষমতা দখলের পর কেবিনেট বলে আর কিছু রইল না। ফলে শিক্ষাসচিবকে বললাম, আমাকে ঠাকুরগাঁও কলেজে বদলি করুন। ততদিনে এটি সরকারি হয়ে গেছে। তিনি অবাক হয়ে গেলেন—‘সবাই ঢাকায় থাকতে চায়, আর তুমি ঠাকুরগাঁও যেতে চাইছ?’ বললাম, ‘সেখানেই বেশি ভালো থাকব। এরশাদের অধীনে কাজ করতে চাই না। ’ সহকারী অধ্যাপক পদে বদলি নিয়ে ফিরে এলাম। বাড়ি থেকে কলেজে গিয়ে শিক্ষকতা করেছি। তখন সরাসরি রাজনীতি না করলেও রাজনীতি আমার মাথায় সব সময় ছিল। শিক্ষক হিসেবে এলাকায় নানা সামাজিক, ক্রীড়া সংগঠন, নাট্য সমিতি, ক্লাব গড়ে তুলেছি। এসব সংগঠন করার উদ্যোগ পরে যখন রাজনীতিতে যুক্ত হলাম, নির্বাচন করলাম, আমাকে খুব সাহায্য করল। আমার স্ত্রী মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য ঢাকায় থাকত। দেড় বছরের ছোট-বড় বোন দুটি হলিক্রসে ভর্তির সুযোগ পেল। ফলে আমাকেও সহযোগী অধ্যাপক থাকার সময় ঢাকায় চলে আসতে হলো। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ‘ডিআইএ (ডিরেক্টরেট অব ইন্সপেকশন অ্যান্ড অডিট)’-এ ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে চাকরি করতাম। ইন্দিরা রোডের একটি ভাড়া বাসায় প্রায় ১২ বছর ছিলাম। তবে এখনো আমি শিক্ষকতা পেশাটি মিস করি। আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় হলো শিক্ষকতাজীবন। আমার কোনো ছাত্র আমাকে শিক্ষক হিসেবে খারাপ বলে না। তার পরও ১৯৮৮ সালে চাকরি থেকে পদত্যাগ করলাম। কারণ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি, রাজনীতিতে যাব।
প্রশ্ন : কেন?
রাজনৈতিক পরিবারগুলোর জনগণের কাছে কিছুু প্রতিশ্রুতি, মানুষের প্রতি কিছু দায়িত্ব থাকে। ফলে নিজের জেলা থেকে আমার কাছে প্রচুর মানুষ আসতে শুরু করল। তারা আমাকে মেয়র পদে নির্বাচনের অনুরোধ করল। আমি তাদের বললাম, সরকারি চাকরিতে তো অনেক বছর হয়ে গেল; কিন্তু তারা তা মানতে নারাজ। তারা অনুরোধ করল, আপনি নতুন রাজনৈতিক জীবন শুরু করুন। ফলে ডিআইএর ডিরেক্টরের কাছে পরামর্শের জন্য গেলাম। তিনি বললেন, ‘ব্যক্তিগতভাবে ক্যারিয়ার গড়তে চাইলে তুমি বড়জোর ডিজি (ডিরেক্টর জেনারেল) হতে পারবে, সে সম্ভাবনা তো নেই; কিন্তু তোমাদের পারিবারিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডল আছে, তোমার ইমেজও ভালো, সেখানে তোমার অনেক সম্ভাবনা আছে। ’ ফলে ১৯৮৮ সালে সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগ করে পৌরসভা নির্বাচন করতে বাড়িতে চলে গেলাম।
প্রশ্ন : বিএনপিতে কেন যোগ দিলেন?
জিয়াউর রহমান সাহেবের রাজনীতি আমাকে আকৃষ্ট করেছে। ব্যক্তিগতভাবে আওয়ামী লীগের রাজনীতি আমার কাছে কখনো পরিষ্কার হয়নি। সুনির্দিষ্টভাবে তারা কী করতে চায়, সেটি আমার কাছে কখনো পরিষ্কার ছিল না। যেহেতু ন্যাপের বড় অংশটিই মশিউর রহমান যাদু মিয়ার নেতৃত্বে বিএনপিতে যোগ দিয়েছিল, ফলে আমরা স্বাভাবিকভাবেই বিএনপির মধ্যে আমাদের একটি ‘অ্যাফিলিয়েশন’ খুঁজে পেয়েছিলাম।
প্রশ্ন : প্রথম নির্বাচনের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?
অন্যদের জন্য নির্বাচন করেছি, ফলে নির্বাচনের অভিজ্ঞতা আমার অনেক পুরনো। কিন্তু নিজের জন্য নির্বাচন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের যে প্রতিক্রিয়া, ভালোবাসা দেখেছি, সেটি ব্যাখ্যা করতে পারব না। এতে আসক্তি ধরে যায়। গ্রামের পাড়াগুলোতেও ভোটের জন্য গিয়েছি। বয়স্ক নারীরা আমাকে আদর করতেন, মুখে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন—এগুলো আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। এরপর তো আমি পৌরসভা নির্বাচনে জিতলাম।
প্রশ্ন : কিন্তু ১৯৯১ সালের পর দুইবার আওয়ামী লীগের প্রার্থীর কাছে সাধারণ নির্বাচনে হেরে গেলেন কেন?
আমার নির্বাচনী এলাকা ‘ঠাকুরগাঁও সদর’ সব সময়ই আওয়ামী প্রভাবিত এলাকা, তাদের আসন। পাশের বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রাণীশংকৈল নিয়ে বাবার সিট। তিনি বরাবরই জিতেছেন। ২৫ বছর পৌরসভা চেয়ারম্যান ছিলেন। ফলে পৌরসভা নির্বাচনে তিনি, আমি ও আমার ছোট ভাই কখনো হারিনি। এ আসনে এবার আমার ছোট ভাই জিতে এসেছে। কিন্তু সদর থানায় ২০টি ইউনিয়ন আছে। সেখানে ভোটারের ৩৫ শতাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। ফলে বাবা আমাকে তাঁর আসন থেকে নির্বাচন করতে বললেও মেয়র হিসেবে আমি সদর আসন থেকেই নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ছাত্রজীবন থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে বলে আমার ধারণা ছিল আমি তাদের ভোটগুলো পাব। কিন্তু নির্বাচনের পর বুঝেছি, ভোটারদের কাছে না গেলে ভালোবাসা সেভাবে তৈরি হয় না। যেহেতু সেখানে খুব বেশি যাতায়াত করতাম না, যদিও তারা জানত, আমি চখা মিয়ার ছেলে; কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে আমি কেমন, সেটি তো জানত না, সাধারণ মানুষ আমাকে ভালোভাবে চিনত না। ফলে তাদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। তাই প্রথমবার নির্বাচিত হতে পারিনি। এ জন্য আমার জিদ বেড়ে গেল। গ্রামে গ্রামে যাওয়া শুরু করলাম। ১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে আমি কিন্তু সাড়ে তিন হাজার ভোটে হেরেছি। তার কারণও আছে—ফররুখ আহমেদ তখন সেখানে পুলিশের এসপি ছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগের কড়া সমর্থক। বিভিন্নভাবে তিনি আমার নেতাকর্মীদের হয়রানি, গ্রেপ্তার করে আমাকে হারিয়ে দিলেন। তবে কখনো হাল ছাড়িনি। এরপর বাড়িতে বাড়িতে যাওয়া শুরু করলাম। ২০টি ইউনিয়নের প্রতিটি বাড়িতে গিয়েছি এবং ভোটারদের সংগঠিত করেছি। ফলে ২০০১ সালের নির্বাচনে প্রায় ৪০ হাজার ভোটে জিতেছি।
প্রশ্ন : সেবার কেন আপনাকে টাকার মালা দেওয়া হলো?
এই অভিজ্ঞতা কোনো দিন ভুলব না। তখন ভোটারদের মধ্যেই প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল যে ‘স্যার গরিব মানুষ, স্যারের টাকা নেই; স্যারকে জেতাতে হবে, আমরাই টাকা দেব। ’ গ্রামের সাধারণ নারীরা তাঁদের জমানো টাকা থেকে এক, দুই, পাঁচ, ১০, ৫০, ১০০ টাকার মালা গেঁথে আমাকে পরিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, আপনার টাকা জোগাড়ের দরকার নেই, আমরাই টাকা দিচ্ছি। এভাবে সেই নির্বাচন করেছি। আমার গোটা রাজনৈতিক জীবনের পুঁজি হলো মানুষের ভালোবাসা। খুব অর্থ বা বিত্ত আমার নেই। আমি খুব সাধারণ মানুষ। এসব সাধারণ মানুষের ভালোবাসা নিয়ে এত দূর এসেছি। কেউ বিশ্বাস না করলেও সত্য—এখনো ঠাকুরগাঁওয়ে দলের জন্য আমাকে কোনো টাকা-পয়সা খরচ করতে হয় না। একটি পয়সাও খরচ করি না। পার্টিকে সেভাবে চালানোর ব্যবস্থা চালু করেছি। কোর্ট, মামলা এখন চলছে, এসবের খরচ দিতে হয়।
প্রশ্ন : সেবার দুই বছর ১০ মাস কৃষি প্রতিমন্ত্রী থাকার সময় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কী কাজ করেছেন?
আমার সবচেয়ে সন্তুষ্টি হলো—আমার উত্তরবঙ্গের কৃষকরা পানির অভাবে সবচেয়ে বেশি ভোগে। সেখানে সেচব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে ‘ডিপ টিউবওয়েল প্রজেক্ট’ থাকলেও কার্যকর ছিল না। প্রায় সাড়ে ৪০০ টিউবওয়েল অকেজো পড়ে থাকত। এরশাদ সাহেব গ্রামীণ ব্যাংকের অধীনে এই প্রজেক্টটি দিয়ে দিলে তারাও চালাতে পারেনি। আমি কৃষি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে প্রকল্পটি বরেন্দ্র বহুমুখী প্রকল্পের অধীনে নিয়ে এলাম। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত এই প্রকল্প এখনো ওই অঞ্চলের সেরা প্রকল্প। বগুড়া পর্যন্ত গিয়ে রাজশাহীর বরেন্দ্র বহুমুখী প্রকল্পের সঙ্গে এটি যুক্ত হয়েছে। ফলে সে অঞ্চলে কৃষি উত্পাদন তিন গুণ বেড়েছে। কৃষকরা এখন স্মার্ট কার্ড দিয়ে প্রয়োজনীয় পানি কেনেন। আমার গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী ইত্যাদি অঞ্চল তো মঙ্গাপীড়িত। কৃষকদের বাড়তি ফসল চাষ করানোর জন্য আমি সেখানকার চরাঞ্চলসহ নানা অঞ্চলে ভুট্টা চাষ শুরু করেছিলাম। এখন সেখানে ভুট্টা উদ্বৃত্ত হয়, কৃষকদেরও অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা হয়েছে।
প্রশ্ন : এরপর বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে কী করলেন?
খুব খারাপ সময়ে আমাকে এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তখন ২০০৪ সাল। হজ ফ্লাইট নিয়ে খুব গোলমাল হচ্ছিল। মীর মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন এর মন্ত্রী ছিলেন। হজ ফ্লাইটগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। হাজিরা কাফনের কাপড় পরে মিছিল করছেন। এর কারণ হলো, টিকিটের দাম ২০০ ডলার করে বেশি চাওয়া হয়েছিল। আরো অনেক সমস্যা হচ্ছিল। এ সমস্যা দিন-রাত পরিশ্রম করে আমরা সমাধান করেছি। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য। এ ছাড়া যাঁরা দীর্ঘকাল বিমানের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা চুরি করা ব্যতীত আর কিছুই করতে পারেননি। একসঙ্গে এক দিনে এক অর্ডারে আমরা চারজন পরিচালককে সরিয়ে দিয়েছি। বিমানের তত্কালীন এমডি ড. এম এ মোমেনের সহযোগিতায় তখন বিমানে অনেক মৌলিক সংস্কার করেছি। যাত্রীসেবা কার্যক্রম বাড়ানোর চেষ্টা করেছি। ফলে বিমান কিছুটা লাভজনক অবস্থায় এসেছে। আমিই ম্যাডামকে (খালেদা জিয়া) বলে অন্য মন্ত্রণালয় থেকে তাঁকে বিমানে এমডি হিসেবে এনেছি। সরকারের শেষ দিন পর্যন্ত এই দায়িত্বে ছিলাম।
সূত্র : কালের কণ্ঠ
Like this:
Like Loading...
Related